মতামত: কেন বাহে আমাক মফিজ কওয়া নাগে
- প্রকাশিত : মঙ্গলবার, ২২ জুলাই, ২০২৫
- ৫১৬ বার পাঠ করা হয়েছে

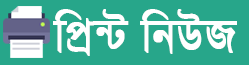
অনলাইন ডেস্ক:
অনেক দিন ধরেই ‘মফিজ’ শব্দটি একটি অবমাননাকর উপাধি হিসেবে রংপুর অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই অপমানজনক উপাধি মূলত দেশের উত্তরের দারিদ্র্যপীড়িত ও অবহেলিত জীবনের প্রতি অবজ্ঞার প্রতীক।
বর্তমানে ‘মফিজ’ শব্দটি সাধারণত বোকার প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ শব্দটির পেছনে আছে একটি জাতীয় ইতিহাসের অংশ, যেখানে দারিদ্র্য ও সংগ্রামকে অঞ্চলভিত্তিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা হয়েছে।
এই শব্দের প্রবল উপস্থিতি রংপুর অঞ্চলের মানুষের প্রতি একধরনের স্থায়ী অবজ্ঞা তৈরি করে, যা বাস্তবতার কাঠামোগত বিশ্লেষণ না করে শুধুই বিদ্রূপের আশ্রয় নেয়। এ প্রবণতা একটি দীর্ঘ ইতিহাসকে আড়াল করে দেয়—ঐতিহাসিক সেই শর্তগুলোকে, যা ঔপনিবেশিক আমল থেকেই রংপুরকে দুর্ভোগ ও বঞ্চনার পথে ঠেলে দিয়েছে।
রাজনীতির ভাষায় মফিজ
‘মফিজ’ শব্দের ব্যবহার কেবল সামাজিক তামাশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাজনীতির মঞ্চেও তার প্রবেশ ঘটেছে। ২০২৩ সালে একটি জনসভায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদ আসাদুজ্জামান নূর উত্তরাঞ্চলের পুরোনো পরিকাঠামোর দুরবস্থা তুলে ধরেন এবং সাবেক বিএনপি মন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে অভিযুক্ত করেন উত্তরবাসীকে ‘মফিজ’ আখ্যা দেওয়ার জন্য। নূর নিজ দল আওয়ামী লীগের উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে সৈয়দপুর বিমানবন্দরের প্রতিদিনের ১৮টি ফ্লাইটের কথা তুলে ধরেন এবং ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘এখন দেশে একটাই মফিজ আছে, সেটা হলো বিএনপি।’
এ ধরনের বক্তব্য ‘মফিজ’ শব্দকে রাজনৈতিক অপদার্থতার প্রতীক হিসেবে স্থাপন করে। অথচ এ ধরনের চটজলদি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক কৌতুক ছাড়িয়ে সামাজিক প্রান্তিকতার প্রতিও একরকম অবহেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।
পানির জমিন: চিলমারীর বাস্তবতা
চিলমারী বাংলাদেশের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল। এখানে ৭৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এই অঞ্চলে বর্ষাকালে তীব্র বন্যা ও ভাঙন বাসিন্দাদের বারবার বাস্তুচ্যুত করে। তারা চরের বাসিন্দা—চরদ্বীপে ঘর বাঁধে, আবার নদী তা ভেঙে নিয়ে যায়। এই নিরবচ্ছিন্ন বাস্তুচ্যুতি আয়রোজগারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দারিদ্র্যের চক্র ভাঙতে বাধা দেয়।
বর্ষাকালে কাজ থাকে না। অক্টোবর থেকে জুনের মধ্যে যা আয় হয়, তা-ই সারা বছরের জন্য টানতে হয়। আগাম ফসলের পূর্বে দেখা দেয় মঙ্গা—একধরনের মৌসুমি দুর্ভিক্ষ। জীবন চলে ‘হাত-মুখ’ চালিয়ে এবং প্রতিবছর নতুন করে সংগ্রাম শুরু হয়। এই বাস্তবতা অনেক পুরোনো—১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষেও চিলমারীর মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই বাসন্তীর ছবি আজও আমাদের চোখে ভাসে।
মফিজ শব্দের উৎস: দুটি আখ্যান
চিলমারী ও ঢাকার চরবাসীর মধ্যে ‘মফিজ’ শব্দটি নিয়ে দুটি গল্প প্রচলিত। প্রথম শুরু হয় ১৯৭০-এর দশকে, যখন একজন উদ্যোক্তা মফিজ চিলমারী থেকে ঢাকাগামী একটি বাস সার্ভিস চালু করেন। এই বাসে করে ঢাকায় কাজ করতে আসতেন অনেক শ্রমিক। তাঁদের হাতে থাকত ‘মফিজ’ সিলযুক্ত একটি চিঠি, যার মাধ্যমে তাঁরা কাজ শেষে আবার ফিরে যেতেন। কালের পরিক্রমায় ‘মফিজ’ হয়ে ওঠে একপ্রকার পরিত্যাজ্য শ্রমিকদের প্রতীক, যাঁদের শুধু কাজের সময় প্রয়োজন, পরে তাঁরা অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু ‘মফিজ’ নামটা টিকে যায়।
দ্বিতীয় একটি সূত্রে জানা যায়, একজন চিলমারীর মফিজ ঢাকায় এসে শহরের বাস্তবতা ও ভাষায় খাপ খাওয়াতে পারেননি। তাঁর সরলতা ও আচরণকে কেন্দ্র করে শহুরে মানুষদের চোখে ‘চরের লোক’ হয়ে ওঠে অজ্ঞ ও সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ। ফলে ‘মফিজ’ একটি গালমন্দ হয়ে ওঠে, যা আসলে একক জীবনের সংগ্রামের নামকে লজ্জায় রূপান্তর করে।
ঔপনিবেশিক ধারা ও চরবাসীর বহির্ভূতকরণ
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন চিলমারীর চরগুলোকে ‘অস্থিতিশীল’, ‘হিংস্র’ ও ‘বেআইনি’ স্থান হিসেবে বর্ণনা করত। ১৯০৭ সালের একটি রিপোর্টে চর অঞ্চলকে বুনো সীমান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা স্থানীয়দের অসৎ বা ধোঁকাবাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ করতেন, এমনকি পথঘাট জিজ্ঞাসার উত্তরে ‘মুই চেঙড়া মানিষ, মুই কী জানু বাবু?’—এই সরল উত্তরকেও তারা ব্যাখ্যা করত অবিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে।
ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই অঞ্চলকে শাসনযোগ্য করার জন্য স্থানীয়দের ভীরু, হিংস্র ও নিয়ন্ত্রণহীন রূপে চিত্রিত করেছিল। চরের জমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে লাঠিয়াল বাহিনীর ব্যবহার, অভিবাসী ভাটিয়া জনগোষ্ঠীর প্রতি সন্দেহ এবং চর এলাকাকে অপরাধের কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন—সবকিছুই এই শ্রেণি বিভাজনের অংশ। এসব গঠনমূলক নিপীড়নমূলক চর্চা এখনো আধুনিক রাষ্ট্র ও নাগরিক চেতনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।
চরবাসীর পরিচয়ের স্তর ও অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য
চিলমারীর মধ্যেও একটি অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস রয়েছে। ‘কায়েম’ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা ও চর অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভাজন আছে। চর অঞ্চলে আবার ‘বাঙাল’ ও ‘ভাটিয়া’ নামে ভাষা ও সংস্কৃতিভেদে পরিচয় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও তারা একসঙ্গে জীবন যাপন করে, বিয়ে করে এবং একে অন্যের দুর্দশা ভাগ করে নেয়।
মূল ভূখণ্ডে বসবাসরত মানুষেরা এই বিভেদ ধরে রাখে। ‘ভাটিয়া’দের মসলা বেশি খাওয়া, চিৎকার করে কথা বলা বা ‘রোহিঙ্গা’ বলার মতো মন্তব্য এই বৈষম্যকে আরও উসকে দেয়। নদীভাঙনের শিকার মানুষদের অপমান করা যেন একধরনের স্বাভাবিক কথাবার্তার অংশ হয়ে গেছে।
ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের বীজ
চরবাসী শুধু ভৌগোলিকভাবে নয়; বরং সাংস্কৃতিকভাবেও ক্রমাগত প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। যাদের আমরা ‘মফিজ’ বলে ডাকি, তারা আসলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমি ক্ষয় ও রাষ্ট্রের অবহেলার সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করে। ‘মফিজ’ শব্দটি একসময় ছিল দৈনন্দিন সংগ্রামের আলামত, আজ তা হয়ে উঠেছে অন্যকে হেয় করার যন্ত্র।
রাজনৈতিক নেতারা যখন এই শব্দ ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ছোট করেন, তখন তা কেবল ব্যক্তিবিদ্বেষ নয়; বরং একটি জাতিগত শ্রেণির প্রতি অসম্মান। মানুষ তাদের ওপর এমনি ক্ষিপ্ত হয়নি; সরকার অনেক গুরুতর সমস্যার মধ্যে বহু ‘অন্য’কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। ‘মফিজ’ শব্দটি একধরনের পরিচয়ের বোধ তৈরি করে, যেখানে ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও বাস্তবতা একক অপরাধে পরিণত হয়।
শহুরে ভদ্রলোকেরা আবার মাঝেমধ্যে জাতীয় ঐক্যের কথা বলে। আমাদের ভাষায় গরিবকে হেয় করা। আমরা যদি ভাষায় এই অবচেতন শ্রেণি বিভাজন ব্যাপারে সতর্ক না হই, তাহলে সামনের অনুমেয় সবচেয়ে বিপদ কী করে মোকাবিলা হবে? জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন বা প্রান্তিক জীবনের বাস্তবতায় অনেকেই উদ্বাস্তু হবেন, চিলমারীর চরসহ সারা দেশের নিচু জায়গা থেকে বহু লোকের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের নাম নিয়ে হেয় করলে বিপদের সময় কি জাতীয় ঐক্য থাকবে?
চরবাসীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি এখন আছে, তা শোধরাতে না পারলে ভবিষ্যতের যেকোনো দুর্যোগেও সমাজ একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবে না এবং এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমস্যা নয়।
ড. সাদ কাশেম ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের লেকচারার সুত্র: প্রথম আলো
এম কন্ঠ/এস/২০২৫
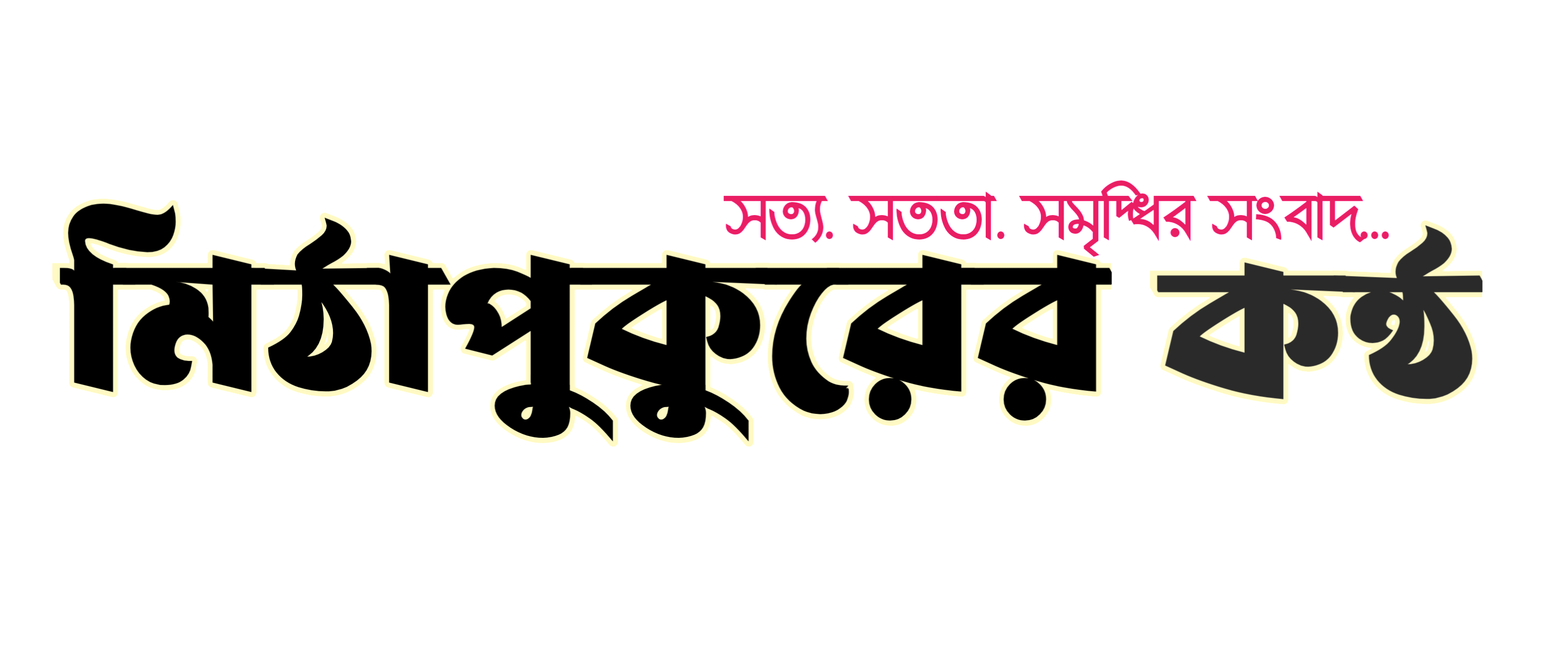
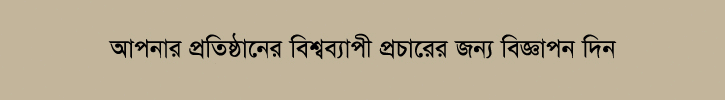
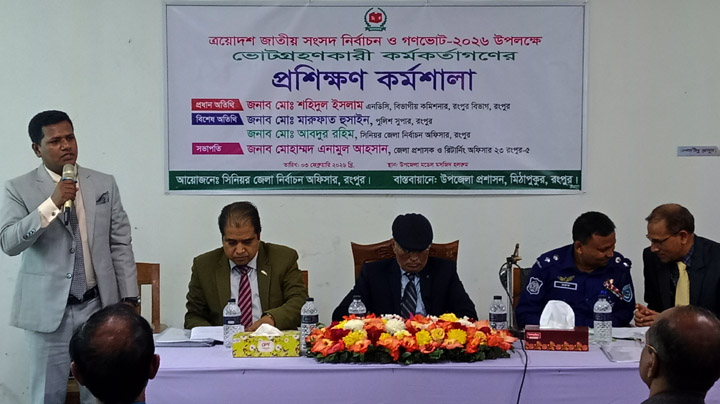









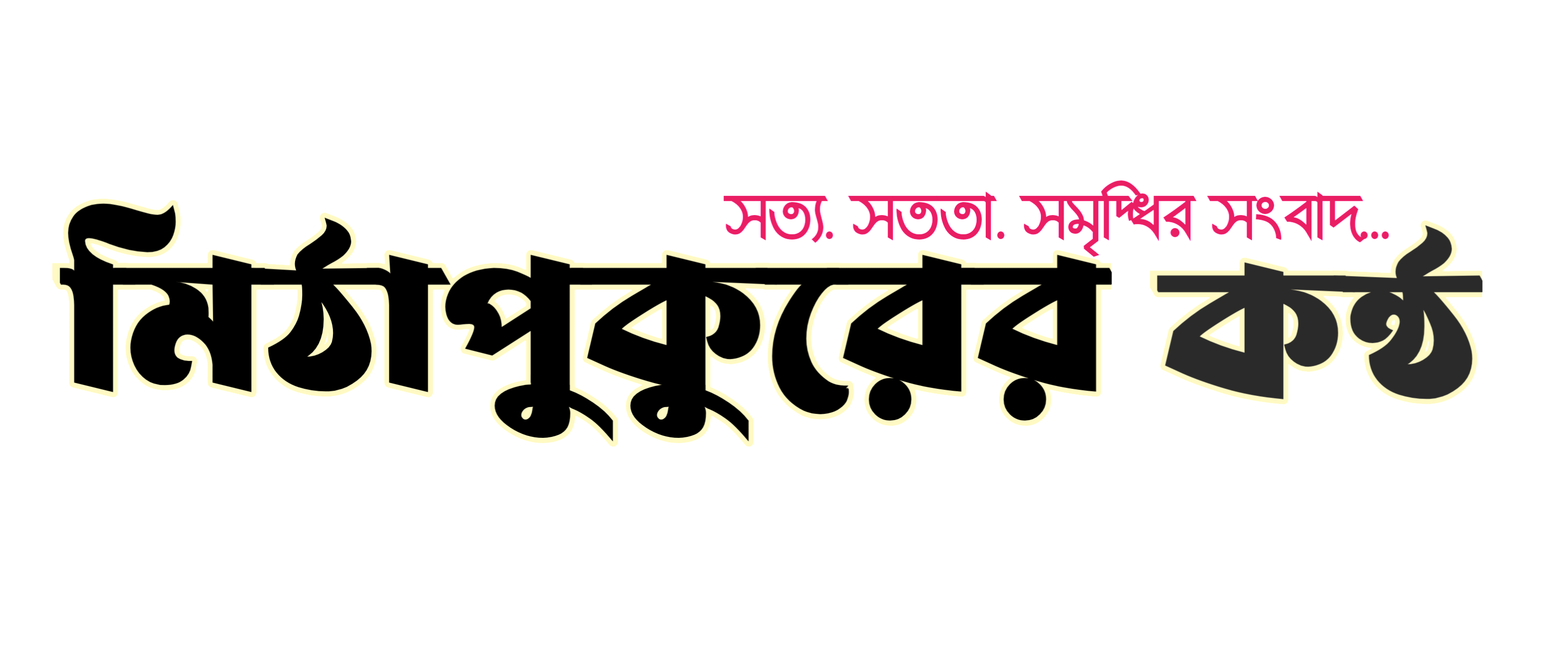
Leave a Reply